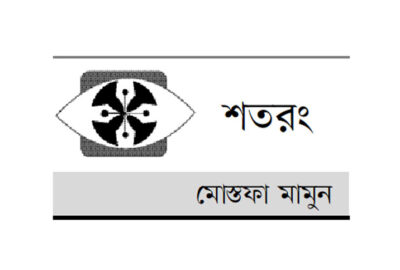নিজের চোখের সামনে ঘটা ঘটনা। হলে মিছিলের জন্য আটকানো হয়েছে ছাত্রদের। উটকো ধরনের ক্যাডাররা পাহারা দিচ্ছে, যাতে কেউ ওদের চোখ এড়িয়ে চলে যেতে না পারে। এর মধ্যে একজন হনহন করে বেরিয়ে গেল এবং কেউ বাধা দিল না। পেছন থেকে বড় নেতা হাঁক দিলেন, ‘এই নবাবজাদা কে রে! মিছিল না করে চলে যায়।’
গেটের পাহারাদারদের একজন জিব কেটে বলে, ‘টিচার। টিচার।’
নেতা একটুখানি থমকান। তারপর পাল্টা জবাব, ‘টিচার হলে কি মিছিল করা যায় না! এখন টিচার আছে, মিছিল করে প্রভোস্ট বানায়া দিমু।’
শিক্ষকরা ছাত্রদের মতো মিছিল হয়তো এখনো করেননি; কিন্তু আমরা বোধ হয় এমন দৃশ্য দেখার কাছাকাছি। উপাচার্য ও প্রশাসন নিজেদের দিন দিন এমন জায়গায় নামাচ্ছে যে পদ-পদবির জন্য তাদের পক্ষে করা অসম্ভব এমন কোনো কাজ আর পৃথিবীতে আছে বলে মনে হয় না।
আমার জীবনে প্রথম কাছ থেকে উপাচার্যকে দেখার ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলের একটা মিটিংয়ে। সাংবাদিক, না ছাত্র হিসেবে উপস্থিত ছিলাম, তা আর মনে নেই; তবে এটা মনে আছে যে ভিসি মহোদয় দুপুরের খাবার আসার পর খাওয়া এবং মিটিং মিলিয়ে একটা রসিকতা করার চেষ্টা করেছিলেন। রসিকতাটি তাঁকে কয়েকবার বলতে হলো। কারণ কেউ ঠিক ধরতে পারছিলেন না, তিনি কী বোঝাতে চাচ্ছেন। এরপর নিজে যখন হো হো করে হাসতে থাকলেন, তখন সবাই বুঝল—এটা রসিকতা ছিল। অবাক লাগল এই দেখে যে তাঁর পর্যায়ের একজন মানুষ সামান্য কয়েকটা বাক্য গুছিয়ে বলতে পারছেন না। এমনকি কেউ যে উপভোগ করছে না, সবাই যে বিরক্ত—এই সামান্য ব্যাপারটাও তাঁর চোখে ধরা পড়ছে না। তিনি নিজেকে নিয়েই মত্ত। মোহভঙ্গ সেদিনই।
আর তাই যখন দেখি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির বিরুদ্ধে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা ইউজিসি দুর্নীতির তদন্তে নামে কিংবা নিজের মেয়ে-জামাইদের নিয়োগ দিতে নিয়োগ পরীক্ষায় যা-তা করেন, ছাত্রলীগের নেতার সঙ্গে ভাগাভাগিতে জড়িয়ে যায় কোনো ভিসির নাম কিংবা সামনের দরজা অবরুদ্ধ বলে পেছনের দরজা দিয়ে কেউ কেউ পালান কিংবা কোনো ভিসি যখন নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য হিসেবে চা আর সমুচার নাম বলেন, তখন অবাক হই না। পুরনো নানা স্মৃতি ভাসে। মনে হয়, এ-ই তো হওয়ার কথা। তাঁরা আরো আরো কী করতে পারেন ভেবে যথেষ্ট বিনোদনও বোধ করি। সত্যি বললে, বিনোদনদাতা হিসেবে তাঁদের অনেকের একটা সামাজিক অবস্থান দাঁড়িয়েছে।
পুরনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্বায়ত্তশাসনের আইন নিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের গর্বের শেষ নেই। কিন্তু সেই আইনের চর্চায় কোথাও কোথাও তো উল্টো দ্বিমুখী ক্ষতি হচ্ছে। এখানে নির্বাচনের মাধ্যমে একটা ভিসি প্যানেল হয় এবং এর শীর্ষ তিনজনের মধ্যে সরকার যেকোনো একজনকে নিয়োগ দেয়। ফলে প্রথমে একজনকে ভোটের মতো একটা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় জিততে হয়। আর বাংলাদেশে ভোটে জেতা, আর যা হোক ফেয়ার প্লে করে সম্ভব না। এর বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে হয়। ওর হাতে ধরতে হয়। ধরলাম এসব করে কেউ একজন নিজেকে যোগ্যতম প্রমাণ করলেন; কিন্তু এতেও শেষ হচ্ছে না। এবার সরকারের উচ্চ পর্যায়ের আশীর্বাদ লাগবে। এর মাধ্যমে তিনি দ্বিতীয় দফা হাত পাতবেন। এই দুই দফা হাত পাতা মানুষগুলোর ব্যক্তিত্ব থাকবে না স্বাভাবিক। তবু এক-দুই দশক আগ পর্যন্ত পদের মর্যাদার কথা ভেবে কেউ কেউ ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করতেন; কিন্তু এখন আর সেসব পদের মর্যাদাটর্যাদার ব্যাপার নেই। সরকার ও সরকারি দলের পক্ষে এমন কোমর বেঁধে নামেন যে মাঝেমধ্যে লজ্জা লাগে। মোটের ওপর উপাচার্যকে সরকারি দলের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার প্রধানের বাইরে আর কিছু আজকাল ভাবতে পারি না।
যেমন কয়েকটা জিনিস ক্ষুদ্র জ্ঞানে ধরতে পারি না। ডিন বা উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন ভোটাভুটিতে হবে কেন? যদি এটা আদর্শ পদ্ধতি হয়, তাহলে তো অন্যান্য ক্ষেত্রেও ভোটাভুটির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যেমন—সচিবালয়ে সচিবদের ভোটে নির্বাচিত হলেন ক্যাবিনেট সচিব। প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের ভোটে নির্বাচিত হবেন এমডি। বিষয়টাকে হাস্যকর মনে হচ্ছে! জ্ঞান এবং বুদ্ধিবৃত্তিসংক্রান্ত কোনো পদে ভোটের মাধ্যমে বসাটা তেমনই হাস্যকর; কিন্তু দেখে দেখে আমাদের গা সওয়া হয়ে গেছে। যেমন এটাও গা সওয়া হয়ে গেছে, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের দলীয় সংগঠনের নামকরণটা হচ্ছে রং দিয়ে। সাদা দল-নীল দল-গোলাপি দল। রংভিত্তিক পরিচয় আমাদের পুরো সমাজেই একটা নিন্দনীয় ব্যাপার বলে গণ্য, অথচ আমাদের মহান শিক্ষকরা সেটাকেই ধারণ করে আছেন সগর্বে। সেই রং দিয়ে বোঝাও আবার খুব সহজ নয়। এক বিশ্ববিদ্যালয়ে নীল হয়তো আওয়ামী সমর্থিত দলের, অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়তো তারা হলুদ। তারা রাগ করলেও বলি, স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ বা জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম জাতীয় সরাসরি নামই বরং ভালো। আমাদের এই রংবেরঙের ঝামেলায় পড়তে হয় না। এটুকু শান্তি তারা চাইলে দিতে পারেন।
পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মানে কাগজে-কলমে দেশের সবচেয়ে বিদ্বান মানুষ। একসময় হয়তো সে রকমই ছিল। এখন আর নেই। আবার একটা কাহিনি। ম্যাট্রিক-ইন্টারমিডিয়েটে স্ট্যান্ড করা এক ছাত্র আমাদের সময় ভর্তি হয়েছে। ওর লক্ষ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হবে। পিএইচডি করবে। শুরুতে যারা এ রকম লক্ষ্য স্থির করে নেয় ওরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়াশোনায় ডুবে যায়। সে-ও ডুবে গেল। এবং ফলও পেল। প্রথম বর্ষে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম। দ্বিতীয় বর্ষ থেকে দেখি মনোযোগ অন্যদিকে। প্রায় প্রতিদিন বিকেলবেলা সেজেগুজে কোথায় যেন যায়! এ-ও খুবই চেনা বিষয়। প্রথম বর্ষে পড়াশোনায় ডুবে যাওয়া ছেলেরা হঠাৎ কোনো নারী দেখে ভেসে ওঠে। এরপর ভেসেই চলে শুধু। ধরা হলো ওকে। সে কিছু বলতে চায় না। তাতে সবাই আরো নিশ্চিত, নিশ্চয়ই গভীর প্রেম।
সে বলল, ‘মোটেও না। আমি আমার লাইনেই আছি।’
‘তাই নাকি। তাহলে রোজ বিকেলে সেজেগুজে কোথায় যাওয়া হয়?’
যা শুনলাম তাতে স্তম্ভিত। ওর এলাকার এক রাজনৈতিক নেতার বাসায় রোজ গিয়ে তাঁর স্তুতি গায়। এক বছর ডিপার্টমেন্টে ঘোরাঘুরি করে বুঝেছে শিক্ষক হতে হলে ফার্স্ট ক্লাসের মতোই দরকার রাজনৈতিক নেতার আশীর্বাদ।
এখানেও একটা টুইস্ট। সেরা ছাত্ররাই শিক্ষক হয়; কিন্তু সব সেরা ছাত্র নয়। সেই সেরারাই শিক্ষক, যাদের রাজনৈতিক বা ভিসি পর্যায়ে বা বিভাগের অভ্যন্তরীণ কাঠামোতে সে রকম যোগাযোগ আছে। অবশ্য ফাঁকফোকর গলে কিংবা অসাধারণ ফল করেও কেউ কেউ ঢুকে পড়ে। কিন্তু শুধু শিক্ষা আর গবেষণায় ডুবে থাকে বলে তাদের শিক্ষকতা জীবন বড় রংহীন। ওরা ভিসি হবে না। ডিন হবে না। নির্ধারক হবে না। কয়েক বছর আগে আমাদের এক বন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ছেড়ে যখন বিদেশে চলে যাচ্ছিল, আমরা কয়েকজন গেছি বোঝাতে। সে মন খারাপ করে বলল, ‘দল করি না, তোষামোদি পারি না। কাজেই কয়েক বছর পর যখন একই পদে ধুঁকতে থাকব, তখন কী হবে?’ এরপর আর কথা বাড়ানো যায়নি।
ওরা চলে যায়। দক্ষরা চুপ করে নিজের কাজে ডুবে থাকে। লাইন-লবিং করা রাজনীতিওয়ালাদের তাতে আরো সুবিধা। এভাবে শিক্ষক হয়ে, আরো লাইন করে, আরো তোষামোদি করে সিঁড়ি ভাঙতে থাকে। এরপর কেউ কেউ প্রভোস্ট-ডিন-ভিসি। এবং তারপর দুর্নীতি-দলবাজি-মোসাহেবির চূড়ান্ত। ‘গাভী বৃত্তান্ত’ বা ‘মহব্বত আলীর একদিন’ জাতীয় গল্পের নায়ক। আহমদ ছফা ও জাফর ইকবালের লেখা এই উপন্যাস দুটি পড়ে নিতে পারেন চাইলে। এই লেখায় জায়গার অভাবে যা যা লেখা গেল না, তার সবই আছে ওখানে।
শেষে আরেকটা গল্প। ২০০১ সালে ক্ষমতায় পরিবর্তনের পর দেরি না করে রাতের বেলায়ই দায়িত্ব নিয়ে নিলেন এক উপাচার্য। কয়েক মাসের মধ্যে ছাত্রী নির্যাতনের ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে ধুন্ধুমার আন্দোলন। সেখানে ছাত্রদের সঙ্গে মানববন্ধনে দাঁড়িয়েছেন সাবেক একজন উপাচার্য। এক তরুণ সাংবাদিকের সঙ্গে তাঁর খুব ভালো খাতির ছিল। সে হাসতে হাসতে বলল, ‘স্যার, আগে সবাই বলত আপনি একাই খারাপ।’
শোনার পর তাঁর লজ্জা পাওয়ার কথা; কিন্তু আনন্দ ও কৌতূহল নিয়ে জানতে চাইলেন, ‘আর এখন কী বলছে?’
‘বলছে সবাই-ই খারাপ।’
উপাচার্য মহোদয় মহাখুশি। সবাই যে তাঁর মতো খারাপ—এর চেয়ে আনন্দের বিষয় যেন আর হয় না।
আবার একদিক থেকে দেখলে এটা মারাত্মক রকম উদারতাও। নিজের নিন্দা শুনেও আমাদের উপাচার্যদের কেউ কেউ মন খারাপ না করে হাসেন। হাসতেই থাকেন।
অতএব, আমরাও হাসি। হাসতেই থাকি।
প্রথম প্রকাশঃ কালেরকন্ঠ
প্রকাশ কালঃ ১১ মার্চ, ২০২১