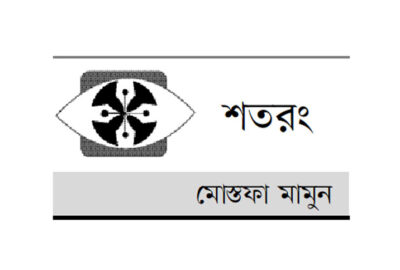অবাক হলাম দেখে যে পুরো শহরে একটাও রিকশা নেই। ঢাকায় যতই ভিআইপি রোডে নিষিদ্ধ হোক, এর বাইরে আজও রিকশার রাজত্ব। সেখানে একটা উপজেলা শহর রিকশাহীন। রিকশা বলতে পেডাল রিকশা নেই, অটো বা ব্যাটারিচালিত রিকশাই শুধু।সাধারণত একটি দেশের রাজধানী বা বড় শহরগুলোতেই যান্ত্রিকতা আর আধুনিকতা বেশি, অযান্ত্রিকতা গ্রাম বা মফস্বলের জন্য বরাদ্দ থাকে। অবশ্য এই দেশে অনেক কিছুই পৃথিবীর থেকে উল্টা। ঢাকায় রিকশার প্রাচীনতা রেখে গ্রামবাংলা যে তলে তলে এমন অত্যাধুনিক হয়ে গেল সে এক রহস্য। পায়ে চালানো রিকশা ভ্রমণের জন্য দারুণ; কিন্তু একই সঙ্গে খুব কষ্টকরও।
বয়সী রিকশাওয়ালা কোনো একভাবে এই কঠিন কায়িক শ্রম থেকে বেঁচেছেন এটা বেশ আনন্দের। যদিও আইনকানুনজনিত কিছু ফেঁকড়া আছে। ব্যাটারির রিকশায় বিদ্যুতের অপচয়ের প্রশ্নও থাকছে। তবু এই যুগে শরীর টানা যান বড় আদিম ব্যবস্থা।কোনোভাবে এর থেকে মুক্তি দরকার।
রিকশাহীনতা একটি চমক; কিন্তু এর চেয়েও বড় চমক হলো স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষার উন্নতি। প্রায় প্রতি ঘরেই উচ্চশিক্ষিত। এ অনার্স শেষ করেছে তো আরেকজন মাস্টার্সের অপেক্ষা করেছে। একজন ইন্টারমিডিয়েট দিচ্ছে তো আরেকজন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার সূচির অপেক্ষায়।যে এলাকার কথা বলছি সেই সিলেট অঞ্চল খুব শিক্ষামুখী নয়, বরং লন্ডনের সঙ্গে সম্পর্কসূত্রে শিক্ষার প্রতি বিরাগই এখানকার একটি সমস্যা। এমন সংস্কৃতিতে শিক্ষামুখিতা বেশ আশা জাগাল। আর এক-দুই দিন পর সেটা নিভেও গেল। কারণ জানা গেল, এই যে এত শিক্ষা, তাতে তেমন কোনো কাজ হচ্ছে না। অনার্স-মাস্টার্স করে ফেলছে বটে; কিন্তু শিক্ষানুপাতিক কাজ বা চাকরি হচ্ছে না। একজন বললেন, ‘শিক্ষায় চাকরি হয় না। চাকরি হয় টাকায়। হয় টাকা, নয় লোক থাকতে হয়।’ ঘুরেফিরে প্রায় সবারই বক্তব্য এক রকম। পড়াশোনা শুধু মান বাড়ায়। কাজে দেয় না একটুও।
মফস্বলের মানুষের জীবনকে দেখার সাধারণ কিছু ভঙ্গি আছে। চাকরি বা কাজের বাজার সম্পর্কেও তাদের বিশ্বাসটা খুবই সোজাসাপ্টা। টাকা ছাড়া চাকরি বা কোনো কাজ হতে পারে—এটা তারা প্রায় বিশ্বাসই করে না। তাদের দোষ নেই। তারা দেখতে পায়, পুলিশ টাকা নিয়ে আসামি ছেড়ে দেয়। জনপ্রতিনিধি টাকা পেলে তবেই কাজ করেন। ইঞ্জিনিয়ার টাকা খেয়ে ঠিকাদারের দুর্বল কাজকে মেনে নেন। এসব ঢাকায় আরো বেশি হয়। কিন্তু ঢাকায় ঠিক দেখা যায় না। একে অন্যকে চেনে না বলে প্রচারিতও হয় না সেভাবে; কিন্তু মফস্বল শহরে কিছুই গোপন থাকে না। মানুষের কৌতূহলও একটু বেশি বলে সবাই সব জেনে যায়।
আর চাকরির বাজার তো সাধারণতই টাকামুখী। টাকার ভিত্তিতে চাকরি লেনদেন হতে দেখে মোটামুটি ধরেই নিয়েছেন এর বাইরে কিছুর সুযোগ নেই। ফলে পড়াশোনার অর্থহীনতা এবং এর প্রতি চাপা বিরাগটাও টের পেলাম। দুঃখের কথাটা শুনে পরিচিত একজন পাল্টা যুক্তি দিল, ‘হবে কিভাবে? সবাই শিক্ষিত। কিন্তু দেখ, অনেকে ঠিকমতো নিজের বিষয়ের নামটাও বলতে পারবে না।’
‘তা হয় নাকি? এত শিক্ষিত।’
‘সব তো অটো পাস।’
‘অটো পাস তো এই করোনার সময়। আগে তো…’
‘এখন ঘটা করে অটো পাস দেওয়া হচ্ছে। আগেও এ রকমই ছিল। মুখে বলত না; কিন্তু ফেল যেন না করে সে রকম চিন্তা ও চেষ্টা সব সময় ছিল। ফলে শিক্ষিত এবং শিক্ষার হার বেড়েছে। কাজেই…’
কিছুটা বোধ হয় ঠিক। মানুষকে শিক্ষামুখী করতে উদারতার দরকার ছিল। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর দেখলেন, পূর্ব পাকিস্তানের পাসের হার খুবই কম। কারণ প্রশ্নপত্র অবিশ্বাস্য রকম কঠিন। তিনি সহজ করার উদ্যোগ নিয়ে প্রবল বাধার মুখে পড়লেন। তবু নাছোড়বান্দা হয়ে কাজটা করলেন; কারণ তাঁর মনে হয়েছিল না হলে মানুষ শিক্ষাবিমুখ হয়ে যাবে। আমাদের ক্ষেত্রেও প্রাথমিক ধারণাটা ঠিক ছিল। সঙ্গে গত এক-দেড় দশকে যোগাযোগ-উন্নয়ন—এসবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও বেড়েছে অনেক। আগে যেখান থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাস করা যেত না, এখন সেখানে মাস্টার্স পর্যন্ত করা যায়। ফলে শিক্ষিত বেড়েছে; কিন্তু অনুপাতে তো আর চাকরি বাড়েনি। তাই কেউ দিচ্ছে শিক্ষার দোষ, কেউ ধরছে ধরাধরির অভাব। দেখে দেখে মনে হলো, সময় এসেছে পুরো বিষয়টা নিয়ে বিশদ ভাববার। শিক্ষিত জনগোষ্ঠী দরকার ছিল। পাওয়া গেছে। এখন শিক্ষাকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে।
প্রথমত, শিক্ষা ও চাকরির অনুপাত ঠিক করতে হলে কারিগরি ও ব্যাবহারিক শিক্ষার সুযোগ বাড়াতে হবে। প্রায় সবাই সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত। সেখানে কাজ নেই। যেখানে কাজ আছে সেখানে আবার সেই ধরনের প্রশিক্ষিত মানুষ নেই।
দ্বিতীয়ত, এখন পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণটা একটু শক্ত করা দরকার। পড়লে আর বসলেই পাসের চক্করে যে শিক্ষিত শ্রেণি তৈরি হচ্ছে, এরা সংখ্যায় বেশি হলে সমাজের জন্য শক্তির বদলে বোঝা। একজন শিক্ষিত মানুষ মানে এলাকায় সম্মানিত। তাঁর মতের-চিন্তার গুরুত্ব আছে। এখন তিনি যদি ভুল ভাবনা ছড়ান, তাহলে সমাজ আক্রান্ত হতে বাধ্য। হয়ও তো বোধ হয়। নইলে এত শিক্ষা বাড়ল; কিন্তু সাংস্কৃতিক পশ্চাদমুখিতা কেন? কেন প্রতিক্রিয়াশীলতা-ধর্মান্ধতা সমান্তরালে বাড়ছে! শিক্ষা তো এগুলো দূরীকরণের জন্য।
ও, আচ্ছা, সার্টিফিকেট আর হার বাড়ানোর শিক্ষা দিয়ে এসব হয় না। শিক্ষা ব্যাপারটা আসলে সহজ-সরল নয়। চাকরি বা কাজ তার একমাত্র কাঙ্ক্ষিত গন্তব্য হলে মুশকিল। শিক্ষা দিয়ে উপার্জনটা একটা বাই প্রডাক্টের মতো, আসল প্রডাক্ট বোধ-রুচি-মানবিকতাসম্পন্ন মানুষ তৈরি। এমন মানুষ তৈরি হলে আসবে যে সমাজ, সেই সমাজ নিজের মতো করে সব সমস্যা ঝেড়ে-মুছে ফেলে দেবে। কিন্তু এই দ্বিতীয় ব্যাপারটা আমাদের সামগ্রিক চিন্তায়ই নেই; এমনকি করোনার সময় এ-ও দেখলাম যে শিক্ষা বিষয়টা আমাদের অগ্রাধিকারেই নেই। বাংলাদেশ কি করোনায় পৃথিবীর সর্বোচ্চ আক্রান্ত দেশ? তা যখন নয়, তখন স্কুল-কলেজ বন্ধ রাখায় কেন সবার ওপরের দিকে। আসলে পড়াশোনা যে ভাবনার ওপরের দিকে নেই এটা তারই প্রমাণ। দোকান খুলতে হবে, না হলে মানুষ না খেয়ে মরবে। ট্রেন চলতে হবে, না হলে জীবন থেমে থাকবে। কিন্তু শিক্ষা না হলেও চলবে; কারণ এতে জীবন-মরণের ব্যাপার তো নেই। এই যুক্তির পাল্টা অনেক যুক্তি ছিল। সেগুলো যে কেউ শুনতে চায়নি; এতেই বোঝা যায় শিক্ষাকে আমরা কী চোখে দেখি। সার্টিফিকেট বিলি করে, পাসের হার বাড়ালেই শিক্ষা হয়ে যায় বলে আমাদের কর্তাব্যক্তিদের ধারণা। কোথায় যে পড়ে আছি! আমূল সংস্কার দরকার। একেবারে আমূল। যেখানে সার্টিফিকেট থাকবে। চাকরি থাকবে। সঙ্গে জ্ঞান এবং মানও থাকবে।
এখন প্রথমটা খুব আছে। দ্বিতীয়টা কমছে। আর তৃতীয়টা প্রায় নেই।
বিশ্ববিদ্যালয়ের হলজীবনের গল্প। এক রুমমেটের দুজন আত্মীয় এসেছেন গ্রাম থেকে। শুয়ে পড়েছেন; কিন্তু ঘুমাতে পারছেন না। কারণ পাশের রুম থেকে কেউ একজন উচ্চৈঃস্বরে পড়ছে, ‘নিকারাগুয়ার রাজধানী মানাগুয়া, প্যারাগুয়ের রাজধানী আসুনসিওন।’ এক আত্মীয় অবাক হয়ে বললেন, ‘নিকারাগুয়া-প্যারাগুয়ে এসব নিয়ে চিৎকার-চেঁচামেচি কেন?’
‘সরকারি চাকরির পরীক্ষা দেবে তো। তার জন্য পড়ছে।’
‘সরকারি চাকরি পেলে নিকারাগুয়ায় পোস্টিং হবে নাকি?’
‘না না। রাজধানী-মুদ্রা এসব আসে তো পরীক্ষায়।’
তিনি আরো অবাক, ‘চাকরি করবে ছাগলনাইয়া-ভূরুঙ্গামারীতে আর জানতে হবে নিকারাগুয়া-প্যারাগুয়ের কাহিনি। অদ্ভুত ব্যাপার তো!’
সহজ-সরল মানুষের সাদামাটা ভাবনা। একভাবে দেখলে তো একেবারে সঠিক ভাবনা। আমরা সব মেনে নিয়েছি বলে এগুলো নিয়ে মাথায় প্রশ্ন আসে না। আসলে তো হাস্যকর।
অন্যজন কথাগুলো শুনছিলেন। তিনি ধরলেন আরেকটা পয়েন্ট, ‘চাকরির পরীক্ষা বুঝলাম; কিন্তু এগুলো তো ক্লাস ফাইভ-সিক্সের পড়া। এসব প্রশ্ন দিয়ে এমএ পাসদের পরীক্ষা হয়! প্রাইমারি স্কুল আর ইউনিভার্সিটির ছাত্র সব দেখি এক হয়ে যাচ্ছে।’
এখনো পুরো হয়নি, তবে হওয়ার পথে। সার্টিফিকেট-চাকরি-শিক্ষার উচ্চহার এই দুষ্টচক্রে আটকে থাকলে সেদিন দূরে নয়, যেদিন দেখবেন যাহাই ক্লাস টু-থ্রি, প্রায় তাহাই মাস্টার্স ডিগ্রি!
প্রথম প্রকাশঃ কালের কন্ঠ, ০৯ সেপ্টেম্বর, ২০২১
লিংকঃ ঘরে ঘরে শিক্ষিত কিন্তু শিক্ষাটা যে কোথায়…